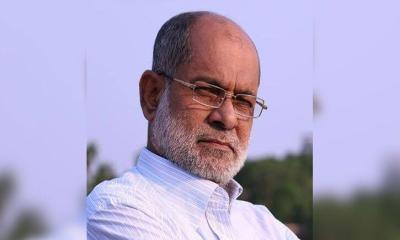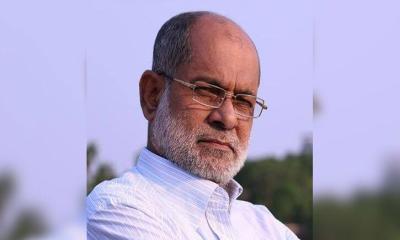অধ্যাপক এবং শিক্ষা আন্দোলন নেত্রী এ এন রাশেদার জন্ম ১৯৪৯ সালের ১ নভেম্বর রংপুর শহরের মুন্সিপাড়ায়। স্কুলজীবন থেকেই শিক্ষা আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন তিনি। ম্যাট্রিক পাসের পর ১৯৬৮ সালে ঢাকায় এসে যুক্ত হন পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে। ১৯৬৯-৭০ সালে ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের সময় ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রী সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন তিনি। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। ১৯৮১ সালে নটর ডেম কলেজে যোগ দিয়ে ২৮ বছর শিক্ষকতার পর ২০০৯ সালে অবসরগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৮৪ সালে তিনি বাংলাদেশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কনভেনশনে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সাল থেকে এ এন রাশেদার সম্পাদনায় প্রকাশ শুরু হয় শিক্ষাবিষয়ক জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা ‘শিক্ষাবার্তা’। করোনা মহামারীর কালে শিক্ষা বাজেট এবং শিক্ষা পরিস্থিতির নানা দিক নিয়ে আগামী নিউজের সঙ্গে কথা বলেছেন অধ্যাপক এ এন রাশেদা।
আগামী নিউজ : অর্থমন্ত্রী এএইচএম মুস্তফা কামাল বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, করোনাভাইরাস সংকটের কারণে প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীর সাধারণ শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবারের বাজেটে শিক্ষা খাতে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। বরাদ্দ আগের চেয়ে বাড়লেও জিডিপির তুলনায় সেটি প্রায় বর্তমান অর্থবছরের মতোই থাকছে। এ বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?
এ এন রাশেদা : শিক্ষা বাজেটে দীর্ঘদিন ধরেই একটা শুভঙ্করের ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষায় বাজেট বেশি দেখানোর জন্য অন্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটও শিক্ষায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এবার শিক্ষা ও প্রযুক্তি মিলিয়ে ৮৫,৭৬০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট বাজেটের ১৫.১০% বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য শিক্ষা খাতে প্রকৃতপক্ষে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৬৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের মাত্র ১১.৬৯ শতাংশ। এটা গত বছরের তুলনায় মাত্র ০.০১ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধির বিবেচনায় প্রকৃত অর্থে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ কমে গেছে। অথচ করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবিলায় এবার একটা বিশেষ শিক্ষা বাজেট ঘোষণা করা প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি। শুধু বাজেট ঘোষণাই নয়, অনেক জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার ছিল।
আগামী নিউজ : শিক্ষা খাতে মোট জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দ রাখা উচিত বলে মনে করে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ‘ইউনেস্কো’। কিন্তু জিডিপির অনুপাতে শিক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় বিগত বহু বছর ধরেই ২ শতাংশের কাছাকাছিই থেকে গেছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় কম। দেশে শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে না কেন। আপনি কী মনে করেন?
এ এন রাশেদা : এটা আসলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা। বিষয়টা বুঝতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। স্বাধীনতার পরপর ১৯৭২-৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার যে শিক্ষা বাজেট অনুমোদন করেছিল সেখানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ২০. ১ শতাংশ। ১৯৭৩-৭৪ সালে সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ২০.৪ শতাংশ। আর এখন মোট বাজেটে ১০ থেকে ১১ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা বাজেটের তুলনায় এখন বরাদ্দ অর্ধেক হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে শিক্ষা বাজেট কমতে থাকে। কিন্তু এরপরও আশির দশকের শুরুর দিকে সামরিক শাসক এরশাদের আমলেও ১১ থেকে ১৩/১৪ শতাংশ বরাদ্দ ছিল। আর এখন একটা গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে এসেও শিক্ষায় এত কম বাজেট বরাদ্দ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আর জিডিপির যে কথা বলা হচ্ছে, সেখানে আমাদের খেয়াল করা দরকার যে, বঙ্গবন্ধুর আমলেই শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল শিক্ষা বাজেটে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে এবং অতিসত্বর সেটা বাড়িয়ে জিডিপির ৭ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এসব তুলনা করে আমাদের বুঝতে হবে স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশক পর শিক্ষা বাজেটে আমরা কতটা পিছিয়েছি। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই শিক্ষা বাজেটে অগ্রগতি হচ্ছে না।
আগামী নিউজ : করোনাভাইরাস মহামারী প্রতিরোধে তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বন্ধ। অনেকেই মনে করছেন সাধারণ ছুটি, লকডাউন ও অন্যান্য জটিলতায় এখন আসলে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরই একটা ‘শিক্ষাবর্ষ নষ্ট’ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ কারণে বিশেষত স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা কেমন সংকটে পড়তে পারে?
এ এন রাশেদা : মহামারীর এই সংকটে আসলে সারা দেশের শিক্ষার্থীরাই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং হবে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অনেক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার আশঙ্কা বেড়ে যাবে। অনেক মেয়েরই হয়তো আর লেখাপড়ায় ফেরা হবে না। বিয়ে হয়ে যাবে। অনেক দরিদ্র কৃষকের ছেলেরা কাজে নেমে পড়বে, স্কুলে ফেরা হবে না। আর শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হওয়ার যে আশঙ্কা, সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। কারণ করোনা পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে সেটাই বলা যাচ্ছে না। তবে আমাদের বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন একটা সংকট দেখা দিয়েছিল। অবশ্য তখন যা করা হয়েছিল সেটা সঠিক বলা যাবে না। একটা শিক্ষাবর্ষের ক্লাস-পরীক্ষা না হওয়া সত্ত্বেও সবাইকে ‘অটো-প্রমোশন’ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন আমাদের ভিন্নভাবে ভাবতে হবে। প্রয়োজনে সময় কমিয়ে এনে হলেও কীভাবে ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়া যায় সেই পথ খুঁজতে হবে।
আগামী নিউজ : মহামারীর কারণে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। শহরাঞ্চলগুলোতে একটা বড় অংশের শিক্ষার্থীর কম্পিউটার-ল্যাপটপ-ফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেও গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে অনলাইন শিক্ষা কতটা কার্যকর বলে মনে করেন?
এ এন রাশেদা : অনলাইন ক্লাস-পরীক্ষা একটা ভালো বিকল্প হতে পারত। কিন্তু আমাদের শিক্ষা কাঠামোকে কি আমরা সে জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছি? সরকার সারা দেশের স্কুল-কলেজে তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। কিন্তু সেই টাকা কোথায় কীভাবে খরচ করা হয়েছে আর সেটা কতটা কাজে লাগছে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি। এসব প্রকল্প যদি ভালোভাবে বাস্তবায়িত হতো তাহলে হয়তো এই সময়ে এসে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতো। আসল কথা হলো অনলাইন ক্লাস-পরীক্ষার জন্য সব শিক্ষার্থীর সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টা ধনী আর দরিদ্রের পার্থক্যের মতোই। যার টাকা আছে সে বেশি খাবে আর যার টাকা নেই সে খাবে না। সমাজের এই পরিস্থিতির সঙ্গে শিক্ষা পরিস্থিতিও একই রকম হয়ে যাচ্ছে। যাদের টাকা আছে তারা ভালো শিক্ষা পাবে, যাদের টাকা নেই তারা শিক্ষা পাবে না। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের কারণে দেশে এই নীতিই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এটা বদলাতে না পারলে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা সব শিক্ষার্থীকে দেওয়া সম্ভব হবে না।
আগামী নিউজ : মহামারীর মধ্যে রাজধানীসহ সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক প্রাইভেট স্কুল-কিন্ডারগার্টেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর প্রকাশিত হচ্ছে। বড় সংকট দেখা দিয়েছে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিয়ে। লাখ লাখ শিক্ষক বেতন-ভাতার অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। এমনিতেই শিক্ষকদের বেতন কম, তার ওপর করোনা পরিস্থিতিতে তাদের জীবিকাই হুমকির মধ্যে পড়ে গেছে। এই সংকট উত্তরণে এমপিও এবং নন-এমপিও বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের সহায়তায় কী করণীয়? আপনি কী ভাবছেন?
এ এন রাশেদা : শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সংকট দীর্ঘদিনের। এখানে একটা অরাজকতা চলছে। এমপিওভুক্ত তো আছেই। আবার স্কুল-কলেজের সরকারি স্বীকৃতি আছে কিন্তু শিক্ষকদের নেইএমন অবস্থাও আছে দেশে! এমন ৮০ হাজার শিক্ষক আছেন যারা স্বীকৃত স্কুলে পড়ান কিন্তু তাদের বেতনের
স্বীকৃতি নেই, অর্থাৎ তারা মান্থলি পে অর্ডার বা এমপিওভুক্ত নন। একই স্কুলে এমপিও ও নন-এমপিও শিক্ষক আছেন। দশকের পর দশক ধরে শিক্ষকদের প্রতি যে অবিচার এই রাষ্ট্র করে যাচ্ছে এখন সেই সবকিছুর ফল আমরা দেখছি। যতভাবে পারা যায় শিক্ষকদের পিষে মারা হচ্ছে। শিক্ষা বাজেটে জিডিপির মতোই শিক্ষকদের বেতন নিয়েও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের সঙ্গে তুলনাটা জরুরি। ১৯৭২-৭৩ সালে একজন হাইস্কুল শিক্ষকের বেতন ছিল ১২০ টাকা। একজন শ্রমিকের বেতন ছিল ৬০ টাকা। তখন এক ভরি সোনার দাম ছিল ৭০ টাকা। অর্থাৎ একজন শিক্ষক তার এক মাসের বেতন দিয়ে দেড় ভরি সোনা কিনতে পারতেন। এখন অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে? এক ভরি সোনার দাম ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকা। এই হিসাবে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতনের তুলনা করলে বোঝা যাবে অবস্থাটা কী! এদেশে শিক্ষকদের বেতন কমেছে, কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে সেই তুলনাটা করলে শিক্ষার প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যাবে।
আগামী নিউজ : আপনি তাহলে বলতে চাচ্ছেন, করোনা মহামারীতে তৈরি হওয়া শিক্ষা ক্ষেত্রের সংকটকে সামগ্রিক শিক্ষা পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়েই বিচার করতে হবে? সেক্ষেত্রে দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রের সামগ্রিক সংকটটা কোথায়? এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী বলে আপনি মনে করেন?
এ এন রাশেদা : একদম ঠিক কথা। করোনা মহামারীতে আমরা যে অবস্থায় পড়েছি সেটা হতো না যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে এত নৈরাজ্য তৈরি করা না হতো। আসলে শিক্ষা তো কেবল সার্টিফিকেট দেওয়ার বিষয় নয়। শিক্ষা হলো মানুষ গড়ার মাধ্যম। যে মানুষ একটা সমাজে একটা রাষ্ট্রে বসবাস করে। ফলে রাষ্ট্র ও সমাজের সংকট থেকে শিক্ষার সংকট ভিন্ন কিছু নয়। এ বিষয়ে প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর একটা বক্তব্য দিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই।
‘আমাদের শিক্ষার সংকট’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : ‘শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছি আমরা, তা শুধু একক ও বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার সংকট নয়। এর সঙ্গে জড়িত আমাদের কৃষির সংকট, শিল্পের সংকট, তথা অর্থনীতির সংকট। আমাদের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত প্রগতিশীল মূল্যবোধকে বিসর্জন দেওয়ার ফলে সৃষ্ট সংকট; তথা রাজনীতির সংকট। সমাজজীবনে দুর্নীতি, উৎকোচ, নারী নির্যাতন, খুন-রাহাজানি-ছিনতাই, কিশোর অপরাধ প্রভৃতির সংকট; তথা সামাজিক সংকট। শিক্ষার সংকট মোচন করতে চাইলে আমাদের সামগ্রিক সংকটের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হবে এবং জাতীয় ভিত্তিতে সুসমন্বিত ব্যাপক কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।’ দুঃখজনক হলেও এটাই সত্যি যে, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে কবীর চৌধুরী শিক্ষা নিয়ে যে কথা বলেছিলেন আমরা এখনো সেই সংকটেই রয়ে গেছি।
আগামীনিউজ/প্রভাত
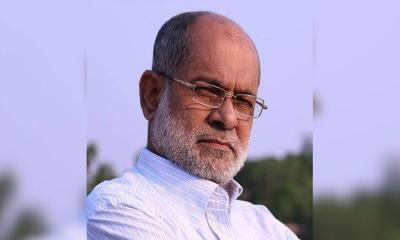
-20251013141837.jpg)
-20251013095452.jpg)

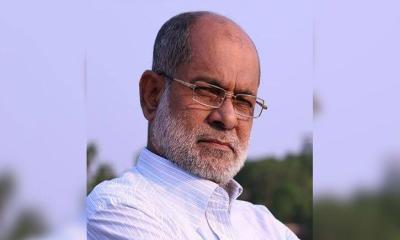

-20250923081410.jpg)